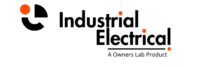লেখক : Dr. Kaustubha Ray
তথ্য সূত্র : লং ড্রাইভ ফ্রম কলকাতা ফেসবুক পেজ
পর্ব : ১
এ এক যুদ্ধের গল্প। কার সাথে কার যুদ্ধ? না হাইড্রোজেনের সঙ্গে বিদ্যুতের যুদ্ধ (Electric vs Hydrogen) যুদ্ধটা অবশ্য ওরা দুজন করছে না। যুদ্ধটা করছি হচ্ছে আমরা।
গল্পটা হল, অনেকেই বলছেন, যে আমাদের মবিলিটির ভবিষ্যৎ আসলে হাইড্রোজেন। আবার আমার মতন কিছু উৎপটাং পাবলিক বলছেন, না না হাইড্রোজেন কিন্তু আসতে এখনো অনেক দেরি আছে। অ্যাকচুয়ালি ভবিষ্যৎ কিন্তু বিদ্যুতেরই হতে চলেছে। এবার এই প্রসঙ্গে আমার একটা গল্প মনে পড়ল। যদি আপনাদের একটু সময় থাকে গল্পটা শুনে নেবেন এবং তাতে হাসা কিন্তু অবশ্যই বাধ্যতামূলক। গল্পটা শুরু করি। এক পাড়ায় দুই পন্ডিত থাকতেন। দুই পন্ডিতেরই বিশাল বিদ্যার ব্যাপার-স্যাপার, মানে একজন বিদ্যার টাইটানিক তো একজন বিদ্যার স্টার লাইনার। এরকম একটা ব্যাপার। তো একদিন সকালবেলা বাজার করতে গিয়ে দুই পন্ডিতের মুখোমুখি দেখা এবং পন্ডিতদের মুখোমুখি দেখা হলেই যেটা হয়, সেটা হচ্ছে একটা তর্ক লেগে যায়। এখানে তর্কটা হচ্ছে যে ব্রহ্মা বড় না বিষ্ণু বড়। এবারে তর্ক তো হেব্বি জমে উঠেছে। কেউই বিভিন্ন বিরাট বিরাট শ্লোক ঝেড়েও ব্যাপারটা সমাধান করতে পারছেন না। তখন তারা ঠিক করলেন যে বাজারে একজন বেশ হোমরা চোমড়া গোছের বাজারওয়ালা বসে তাকে গিয়ে ধরা যাক। কে বড় সে এবারে যেটা বলবে সেটা নিয়ে না হয় চিন্তা করা যাবে। যখন সেই দুই পন্ডিত ওই বাজার ওয়ালার কাছে গিয়ে পৌঁছলেন তখন প্রশ্নটা শুনে বাজারবালা ২ পন্ডিতকেই পা থেকে মাথা অব্দি সুন্দর করে মাপলেন। তারপরে জলদগম্ভীর কণ্ঠে বললেন শুনুন দাদা, ব্রম্মাও আমার পাড়ায় থাকে না বিষ্ণু ও আমার পাড়ায় থাকে না। সুতরাং বলতে পারব না যে কে বড়।
ভবিষ্যৎ কি ?
এবারে মরাল অফ দ্যা স্টোরি যেটা হল সেটা হল ভবিষ্যৎটা আপনিও দেখেননি, ভবিষ্যৎ তা আমিও দেখিনি। কিন্তু আমরা সেটা নিয়ে একটা বিশাল লড়াই করে বসে আছি, তাও আবার নিজেদের ভেতরে। তবে মোটামুটি কিছু কিছু তথ্য থেকে আমরা একটা ট্রেন্ড পাই ভবিষ্যতের সেটা থেকে বলতে পারি যে কি হতে চলেছে বা কি হতে পারে।
এবারে আসি হাইড্রোজেন এর ব্যাপারে। হাইড্রোজেন একটা খুব কাজের গ্যাস এটা দিয়ে অনেক কাজ করা যায়। বিশেষত আমরা যারা চিন্তাভাবনা করছি ভবিষ্যৎ মোবিলিটির ব্যাপারে সেটা তে হাইড্রোজেনের একটা ভূমিকা থাকবেই এটা মোটামুটি আমরা নিশ্চিত। কিন্তু হাইড্রোজেনের কতগুলো প্র্যাকটিক্যাল অসুবিধা আছে, যে প্রাকটিক্যাল অসুবিধা গুলো কিন্তু আমরা খুব তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠতে পারব বলে মনে হয় না। এটা নিয়ে কথা বলার আগে আমরা এনার্জি ডেনসিটি বলে একটা জিনিসকে নিয়ে একটু আলোচনা করব এনার্জি ডেনসিটি হল এমন একটা ব্যাপার যেখানে আপনি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ভরকে ব্যবহার করে কতটা শক্তি পাচ্ছেন সেটা ঠিক করা হয়। ধরা যাক একটা ব্যাটারির ওজন হচ্ছে এক কেজি। সেটা থেকে আপনি এক কিলোওয়াট কারেন্ট পেলেন। এবার দেখা যাচ্ছে আরেকটা ব্যাটারির ওজন এক কেজি কিন্তু সেটা থেকে আপনি দু কিলো ওয়াট কারেন্ট পেলেন। তার মানে হল দ্বিতীয় বাটারিটার এনার্জি ডেনসিটি প্রথম ব্যাটারির দ্বিগুণ। এবারে আমরা আসি বিভিন্ন জ্বালানির এনার্জি ডেনসিটি নিয়ে। এখনো অব্দি দেখা গেছে যে সব থেকে ভালো যে ব্যাটারি পৃথিবীতে তৈরি হয়েছে তার এনার্জি ডেনসিটির তুলনায় পেট্রলের এনার্জি ডেনসিটি প্রায় কুড়ি গুন বেশি। কিন্তু তাহলে পেট্রোলকে ছেড়ে দিয়ে আমরা ব্যাটারি ব্যবহার করবো কেন? কারনটা হচ্ছে দুটো। এক নম্বর হচ্ছে পেট্রল যত রিফাইন করাই হোক না কেন সেটা পুড়ে কার্বন মনোক্সাইড কার্বন-ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড এই সমস্ত গ্যাস গুলো তৈরি করবে। কিন্তু ব্যাটারীতে সেই প্রবলেমটা নেই। দ্বিতীয় কারণটা হচ্ছে যে কোন ইঞ্জিনের এফিশিয়েন্সি অর্থাৎ আপনি কতটা জ্বালানি পুড়িয়ে কতটা শক্তি পাচ্ছেন সেই হিসেবে যদি আপনি দেখতে চান তাহলে দেখবেন পেট্রোল ইঞ্জিনের এফিশিয়েন্সি খুব একটা আশাপ্রদ নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেটা তিরিশের ঘরে থাকে। মানে আপনি যদি ১০০ ওয়াট শক্তি উৎপাদন করেন তাহলে দেখা যাবে যে তার থেকে আপনার চাকায় পৌঁছাচ্ছে মাত্র 30 ওয়াট, আর বাকিটা শব্দ শক্তি, তাপ শক্তি ইত্যাদিতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ইলেকট্রিকের ক্ষেত্রে কিন্তু এফিসিয়েন্সি ৯০ ভাগ বা তার বেশি হয়। সেই জন্য দেখা যাচ্ছে কি মানুষ আইসিই ইঞ্জিন ছেড়ে বিদ্যুতের মোটর এর দিকে ছুটছে। ঠিক সেই কারণেই বর্তমানে ভারতের টোটাল রেল লাইনের ৯২% ইলেকট্রিফিকেশন কমপ্লিট হয়ে গেছে, যেটা গোটা পৃথিবীতে একটি রেকর্ড। এবং ডিজেল ইঞ্জিন তৈরি করা ধীরে ধীরে কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে তার বদলে ইলেকট্রিক ইঞ্জিন তৈরি করার উপরে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে।
এবারে প্রশ্ন আসতে পারে যে তাহলে ব্যাটারির এনার্জি ডেন্সিটি বাড়ানো যাচ্ছে না কেন? বাড়িয়ে তো দেওয়াই যেতে পারে। কিন্তু টেকনিক্যালি এটা একটু এখনো অব্দি অসুবিধা জনক। তবে চীনের বিওয়াইডি বা ক্যাটেল কম্পানি এমন ব্যাটারি বর্তমানে তৈরি করেছেন, যেটি দশ মিনিটের ভেতরে বা পাঁচ মিনিটের ভেতরে শূন্য থেকে 90% চার্জ নিয়ে নিতে পারে। এই ব্যাটারীতে সলিড ইলেকট্রোলাইট ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এখানেও একটা অসুবিধা রয়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে ব্যাটারির এনার্জি ডেন্সিটি মারাত্মকভাবে বেড়ে যাওয়ার জন্য ব্যাটারিকে ঠান্ডা রাখা বা যত্নে রাখার একটা প্রয়োজনীয়তা কিন্তু বারে বারে থেকে যাচ্ছে। এটা যদি না করা হয় তাহলে বিস্ফোরণের একটা সমূহ সম্ভাবনা থেকেই যায়।
একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে আপনাদেরকে বোঝাই ধরা যাক এক কেজি বারুদকে আপনি উঠোনে শুকোতে দিয়েছেন। সেই ক্ষেত্রে কোনোভাবে যদি সেই বারুদে আগুন লেগে যায় তাহলে সেই বারুদটা খুব বেশি ক্ষতি করবে না, বড়জোর জ্বলে শেষ হয়ে থামবে। কিন্তু আপনি ওই এক কেজি বারুদ কে একটা ভয়ংকর চাপের ভেতরে কৌটার ভেতরে রেখে দিয়েছেন, সে ক্ষেত্রে যদি আগুন লাগে তাহলে যে বিস্ফোরণ টা ঘটবে সেটা কিন্তু মারাত্মক আকার ধারণ করবে। এমনকি বাড়িঘর এবং জীবনের বিভিন্ন রকম লোকসান সে করতে পারে। লো ডেনসিটির ব্যাটারি সেই কারণে কম ক্ষতি করে বা হাইডেনসিটির ব্যাটারি সেই কারণে কিন্তু মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে।
এবারে আসি হাইড্রোজেন এর কথায়।
এক নম্বর তুলনায় আসি।
হাইড্রোজেন যেভাবে কাজ করে গাড়িতে, সেটা হল ফুয়েল সেল হিসেবে। অর্থাৎ হাইড্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেনের একটা বিক্রিয়া হয় এবং সেই বিক্রিয়ার ফলে রিভার্স ইলেকট্রোলাইসিস প্রসেসে বিদ্যুৎটি তৈরি করা সম্ভব হয়। এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল সুতরাং এই কারণে যে কোন হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল গাড়ির দাম অত্যন্ত বেশি এবং সেটির রক্ষণাবেক্ষণ ও কিন্তু অত্যন্ত বেশি। এছাড়াও এই গাড়ির সাইলেন্সার দিয়ে জলীয় বাষ্প নির্গত হয়। আপনারা কিন্তু জানেন যে আমাদের পৃথিবীতে গ্রীন হাউস গ্যাস ইফেক্ট এর জন্য জলীয় বাষ্পের কিন্তু একটা ভয়ংকর ভূমিকা আছে। জলীয় বাষ্প কোথাও যদি খুব বেশি বেড়ে যায় সেটাও কিন্তু পৃথিবীর পক্ষে খুব একটা মঙ্গলজনক ব্যাপার নয়। আবার আসি পার্টস এর সংখ্যা ব্যাপারটা নিয়ে, একটা হাইড্রোজেন গাড়িতে প্রচুর পরিমাণ পার্টস থাকে। এবং ঠিক যে কারণে একটা পেট্রোল গাড়িতে যে পরিমাণ পার্টস থাকে সেই তুলনায় সম শক্তির একটা ইভিতে অনেক অনেক কম পার্টস থাকে। সুতরাং খারাপ হওয়ার সম্ভাবনাটাও সে ক্ষেত্রে অত্যন্ত কম। সুতরাং মেন্টেনেন্স এর দিক দিয়ে কিন্তু ইভি অনেক বেশি এগিয়ে।
দু’নম্বর তুলনা :
পার্টস কম থাকার জন্য এবং সরল টেকনোলজি হওয়ার জন্য ইভির মেইনটেনেন্স এবং সারানো হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল গাড়ির তুলনায় অনেক অনেক সস্তা এবং প্র্যাকটিক্যাল।
তিন নম্বর তুলনা:
হাইড্রোজেন অত্যন্ত দাহ্য একটা গ্যাস এবং সেটাকে ট্যাংকের ভেতরে অত্যন্ত উচ্চ চাপে ভরা হয়। ফলে ব্যাটারির তুলনায় হাইড্রোজেনের আগুন লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু অনেক বেশি থাকে। একটা ব্যাটারির গাড়িতে আগুন লাগলে আপনি সময় পাবেন সেই জ্বলন্ত গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার কিন্তু একটা হাইড্রোজেন এর গাড়িতে যদি হাইড্রোজেন ট্যাংকে আগুন লাগে তাহলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আপনি একটি বিশাল বিস্ফোরণের মধ্যখানে নিজেকে আবিষ্কার করবেন। সুতরাং নিরাপত্তার ব্যাপারটা কিন্তু একটা বড় ব্যাপার থেকেই যায়।
চার নম্বর তুলনা:
হাইড্রোজেনকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া একটা বড্ড ঝামেলার কাজ। কারণ হাইড্রোজেনকে তরল অবস্থায় নিয়ে যেতে গেলে সব সময়তেই সাপ্লাই চেনে মাইনাস ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাকে ঠিক করে রাখতে হবে যেটা কিন্তু একটা বেশ কষ্টসাধ্য কাজ। এরপরেও হাইড্রোজেন ডিসপেন্সিং পাম্প যেখানে সেখানে বসানো যায় না। সেটা বসাতে গেলেও বেশকিছু স্পেশাল জিনিসপত্র লাগবে। যেখানে ইভি চার্জার যে কোন জায়গাতে বিদ্যুৎ সংযোগ ঠিক মতন পাওয়া গেলেই বসানো যায় এমনকি সৌর বিদ্যুতের সাহায্যে চার্জার চালানো মোটেই কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। সুতরাং হাইড্রোজেন ফিলিং স্টেশন তৈরি করতে যে খরচা সময় জমি এবং কারেন্ট লাগবে সেই তুলনায় ইভি চার্জার বসাতে অনেক কম রিসোর্স লাগবে।
পাঁচ নম্বর তুলনা:
হাইড্রোজেন তৈরি করতে যথেষ্ট পরিমাণ ইলেকট্রিক লাগে। কারণ জলের ইলেকট্রোলাইসিস করে আমরা হাইড্রোজেন তৈরি করতে পারি। সে ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে যে এই যে বিদ্যুৎটা আমাদের দেশে পুরোটাই কিন্তু এখন অব্দি সোলার বা অচিরাচরিত শক্তি থেকে আসতে পারছে না। অর্থাৎ গ্রীন হাইড্রোজেন তৈরি না করতে পারলে শুধুমাত্র হাইড্রোজেন তৈরি করার জন্য একটা বিশাল দূষণের সম্মুখীন আমাদের কি হতে হবে, যেটাকে পরোক্ষ দূষণ বলে। সে ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন গাড়ি চালাবার মূল উদ্দেশ্যটাই কিন্তু ব্যর্থ হয়ে যাবে। টিভিতেও এই পরোক্ষ দূষণ হয় কিন্তু মোট হিসেব করে দেখা গেছে যদি একটা ইভি পুরোপুরি তাপবিদ্যুৎ শক্তি দিয়েও চার্জ করা হয় তাহলেও সে সারা জীবনে একটা পেট্রোল গাড়ি থেকে ৪৬ পারসেন্ট অবধি কম দূষণ করতে পারে। যদি কেউ এই ব্যাপারটা সম্পর্কে আরও বেশি জানতে চান তাহলে ইপি এর ওয়েবসাইট ঘেঁটে দেখতে পারেন।
৬ নম্বর তুলনা:
ধরা যাক আপনি কোথাও যাচ্ছেন মাঝপথে আপনার গাড়িতে হাইড্রোজেন শেষ হয়ে গেছে। তখন কি আপনি কোন গ্রামে গিয়ে বলতে পারবেন যে দাদা এক বোতল হাইড্রোজেন দিনতো, আমি আমার গাড়িটাতে একটু ঢেলে চালু করি। সেটা কিন্তু কোন ভাবেই সম্ভব নয়। সেই ক্ষেত্রে আপনাকে রোড সাইড অ্যাসিস্ট্যান্ট বা আর এস এর শরণাপন্ন হতে হবে। কিন্তু এরকম বহুবার বহুজনের ক্ষেত্রে হয়েছে, যে ইভির চার্জ শেষ হয়ে যাওয়াতে কোন গ্রামের বাড়ি, কোন হোটেল, কোন কোথাও থেকে একটা প্লাগ পয়েন্ট থেকে একটু তার টেনে নিয়ে গিয়ে গাড়ি চার্জ করে আবার চালু করা গেছে।
কিন্তু তা বলে কি হাইড্রোজেন আমাদের দরকার নেই? অবশ্যই আছে। কিন্তু সেটা ছোট গাড়ির ক্ষেত্রে নয়। বড় গাড়ি বা এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন কিন্তু নতুন করে একটা দিশা দেখাতে পারে। সেই জন্য আমি বলি কি প্রথমেই হয়তো বিদ্যুতের যুগটাই আমাদের কাছে আসবে। কারণ ব্যাটারি টেকনোলজি যেভাবে উন্নত হয়ে চলেছে আগামী দিনটা খুব বেশি দূরে নেই যখন একটা ব্যাটারিকে পাঁচ মিনিট বা দশ মিনিটের ভিতরে পুরো চার্জ করে ফেলা যাবে এবং সেটা যথেষ্ট পরিমাণ বেশি আমাদেরকে রেঞ্জ দেবে। যেমন রকেটের ক্ষেত্রেও কিন্তু জ্বালানি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সেই জ্বালানি আপনার গাড়ি বা মোটরসাইকেলের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় না। তার মানে কি রকেট জ্বালানি দরকার নেই? তা নয়। অবশ্যই আছে। কিন্তু সেটা রকেটের ক্ষেত্রে আছে, রোজকার ইউজের ক্ষেত্রে নেই। সেরকম ভাবেই হাইড্রোজেন অবশ্যই আমাদের দরকার আছে কিন্তু রোজকার ব্যবহারের জন্য হাইড্রোজেন ততখানি সুবিধা জনক হবে বলে আমার মনে হয় না। ঠিক যে কারণেই নরওয়েতে হাইড্রোজেন হাইওয়ে প্রজেক্টটা কে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে এবং সেই জায়গাতে ইভি বা বৈদ্যুতিক যানবাহনকে প্রায়োরিটি দেওয়া হয়েছে।
আমি অফিস থেকে ফিরছিলাম, আর মোবাইলের চার্জ প্রায় শেষের পথে। জিপিএস ছাড়া অজানা রাস্তায় চলা একেবারেই অসম্ভব। ঠিক তখনই মনে পড়ল, কিছুদিন আগে গাড়ির গ্লাভ বক্সে একটা নতুন চার্জার রেখে দিয়েছিলাম— Duracell 38W Fast Car Charger Adapter!
আমি দ্রুত গ্লাভ বক্স খুললাম, চার্জারটা বের করলাম, আর গাড়ির পাওয়ার সকেটে লাগিয়ে দিলাম। মুহূর্তের মধ্যে মোবাইলের স্ক্রিনে ‘Fast Charging’ লেখা ভেসে উঠল। ২০ওয়াটের টাইপ-সি পিডি ও কোয়ালকম সার্টিফায়েড ৩.০ প্রযুক্তি—সত্যিই অসাধারণ! মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই মোবাইলের চার্জ ৫০% ছুঁয়ে ফেলল।
আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। যদি এই চার্জার না থাকত, তাহলে হয়তো মাঝরাস্তায় থেমে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হতো। Duracell-এর এই দ্রুত চার্জিং প্রযুক্তি আমাকে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিল।
আমি গাড়ির স্পিড বাড়ালাম, বাড়ির পথ ধরলাম, আর মনে মনে ভাবলাম—একটা ভালো কার চার্জার থাকা কতটা জরুরি, সেটা আজ হাড়ে হাড়ে টের পেলাম!
আবার বলছি সবকিছুই দরকার। কিন্তু সবকিছুই জেনে বুঝে ঠিকমতন জায়গায় ব্যবহার করাটাই কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য। প্রচুর মানুষ আছেন যারা কিন্তু ইভি মারাত্মক দূষণ করে বলে এখনো চিৎকার করে যাচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলি যে আপনারা কি এই ইন্ডাস্ট্রিটার এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট ভালোভাবে জেনে বা বুঝে চিৎকারটা করছেন? তা কিন্তু নয়। হয়তো ইউটিউবে দেখেছেন পাঁচজন এটার এগেনস্টে বলছেন, google খুললে পক্ষে এবং বিপক্ষে প্রচুর মতামত আপনি পেয়ে যাবেন। সব ক্ষেত্রে যে বিপক্ষের মতামত গুলো সত্যি সেটা কিন্তু নয়। এবং তারা অনেক ক্ষেত্রেই ছদ্ম ডেটা বা সিউডো ডেটা ব্যবহার করছেন। এগুলো কিন্তু সুকৌশলে আপনার অভিমুখটা ঘুরিয়ে দেওয়ার প্রয়াস মাত্র। কই তারা তো একবারও বলছেন না যে সমুদ্রের ড্রিলিং করার কারণে আমরা সমুদ্রের জীববৈচিত্রের এতখানি ক্ষতি করেছি। ওই তেলটাকে তুলে রিফাইনারিতে পাঠাতে আমরা এতখানি ক্ষতি করেছি। এবং এতখানি কার্বন নিঃসরণ করেছি। একবারও বলছেন না একটা রিফাইনারিতে রিফাইন করার প্রসেসের কারণে আমরা প্রচুর পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড কার্বন মনোক্সাইড এবং আরো বিষাক্ত গ্যাস বায়ুমন্ডলে ছড়িয়ে দিয়েছি। এবং ওই তেলটাকে রিফাইনারি থেকে পাম্পে পাঠানোর মধ্যিখানেও আমরা প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি করে চলেছি। কোথাও সেটা বলা হচ্ছে কি? যদি সত্যি কারের এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট স্টাডি করেন তাহলে কিন্তু এদের এই ছদ্ম মুখোশগুলো কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই খসে পড়বে। কিন্তু মজা হচ্ছে কি যারা বলে যাচ্ছেন তারা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, আবার বলছি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গুগল দেখছেন তার নিজের ধারণার সাথে মিলাচ্ছেন আর চিৎকার করছেন। একজন তো দেখলাম লিখেছেন বৈদ্যুতিক গাড়ির মোটর তৈরি করতে রেয়ার আর্থ মিনারেল লাগে। এই তথ্যটা উনি কোত্থেকে পেলেন এটা আমার একটু জানতে মন চায়। আদপে রেয়ার আর্থ মিনারেল বলতে কী বোঝায় সেটা কি উনি বুঝেছেন বলে আমার ধারণা নেই। আর উনি যদি বলেন যে তামা, অ্যালুমিনিয়াম, সিসা, দস্তা, এবং লোহা যদি রেয়ার আর্থ মিনারেল তাহলে সেক্ষেত্রে আমারও কিছু বলার নেই। আসলে লিথিয়াম ব্যাটারির ক্ষেত্রে রেয়ার আর্থ মিনারেল ইউজ করা হয়। মটরের ক্ষেত্রে নয় এই জিনিসটা সম্ভবত উনি গুলিয়ে ফেলেছেন। বর্তমানে লিথিয়াম এর উপরে নির্ভরতা ক্রমেই কমে আসছে সেই জায়গাটা নিচ্ছে সোডিয়াম আয়ন ব্যাটারি। সোডিয়াম নিষ্কাশন করতে কিন্তু লিথিয়ামের থেকে অনেক কম দূষণ হয়।
আবার বলছি ইভি যদি এতই পরিবেশের দূষণ করতে থাকে, তাহলে আমাদের ভারতবর্ষে যে ইলেক্ট্রিফিকেশন করা হয়েছে পুরো রেলওয়েজের। সেটা বন্ধ করে দিয়ে আবার ডিজেল ইঞ্জিনের যুগে ফিরে গেলেই হয়। সেটা তে সবাই রাজি আছেন তো?
আজ এইটুকুই। পরের বারে আবার মাঠে নেমে পড়বো কিছুদিনের মধ্যেই।